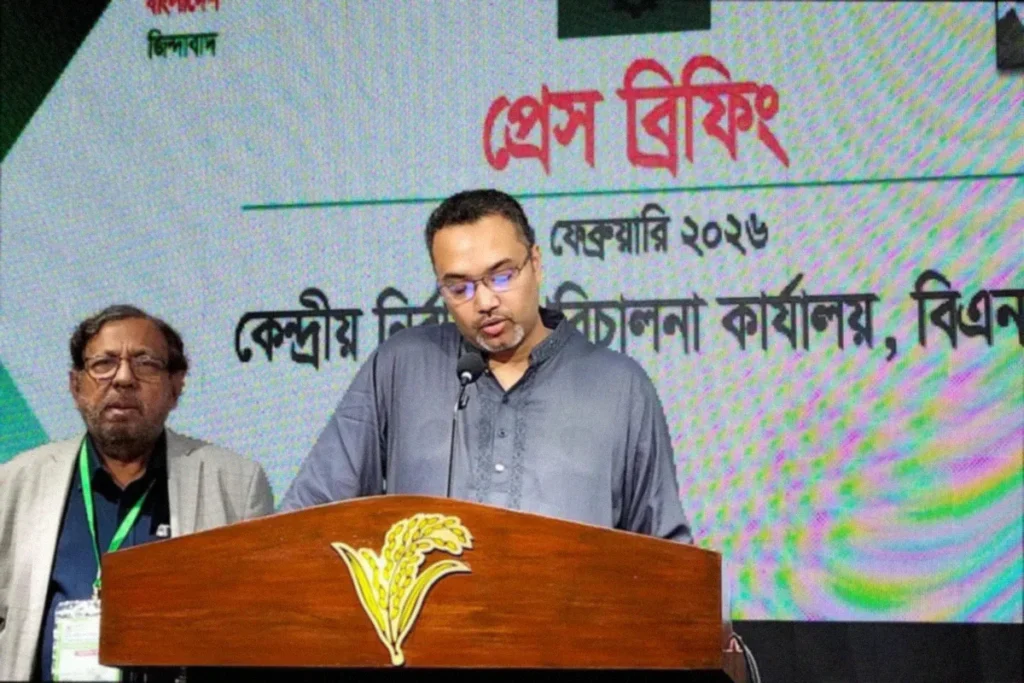জুলাই সনদ বাস্তবায়নসহ চারদফা দাবিতে আন্দোলনের ঘোষণা দিয়েছে জামায়াতে ইসলামী (Jamaat-e-Islami)। গতকাল মগবাজারের আল ফালাহ মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে এ কর্মসূচি জানান দলের নায়েবে আমির ডা. সৈয়দ আব্দুল্লাহ মোহাম্মদ তাহের। শুরুতে আট দল নিয়ে যুগপৎ আন্দোলনের পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি), আমার বাংলাদেশ পার্টি (এবি) ও গণঅধিকার পরিষদ সরে দাঁড়ায়। অন্যদিকে একই দাবিতে পৃথকভাবে কর্মসূচি দিয়েছে চরমোনাই পীরের দল ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ (Islami Andolon Bangladesh), মাওলানা মামুনুল হকের নেতৃত্বাধীন বাংলাদেশ খেলাফত মজলিস, মাওলানা আবদুল বাছিত আজাদ ও আহমদ আব্দুল কাদেরের নেতৃত্বাধীন খেলাফত মজলিস। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশ এই সমন্বিত নড়াচড়াকে রাজনৈতিক সুবিধা আদায়ের চাপসৃষ্টির কৌশল হিসাবে দেখলেও বেশ কিছু বিশ্লেষক এটাকে ‘ভারতীয় এজেন্ডা’ বাস্তবায়নের নতুন তৎপরতা হিসেবে মনে করছেন।
জুলাই জাতীয় সনদ ও পিআর (Proportional Representation) পদ্ধতিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচনসহ পাঁচ দফা দাবি আদায়ে এই মাসেই তিন দিনের কর্মসূচি দিয়েছে জামায়াত—১৮ সেপ্টেম্বর ঢাকায় সমাবেশ ও বিক্ষোভ মিছিল, ১৯ সেপ্টেম্বর সব বিভাগীয় শহরে বিক্ষোভ, আর ২৬ সেপ্টেম্বর দেশের সব জেলা-উপজেলায় সমাবেশ। দাবিগুলো হলো: (১) জুলাই জাতীয় সনদের ভিত্তিতে আগামী ফেব্রুয়ারিতে নির্বাচন আয়োজন, (২) সংসদের উভয় কক্ষে পিআর পদ্ধতি চালু, (৩) সবার জন্য ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড’ নিশ্চিত, (৪) ‘ফ্যাসিস্ট’ সরকারের জুলুম-গণহত্যা ও দুর্নীতির বিচার দৃশ্যমান করা, (৫) ‘স্বৈরাচারের দোসর’ জাতীয় পার্টি ও ১৪ দলের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করা। একই কর্মসূচি পৃথকভাবে ঘোষণা করেছে ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ ও খেলাফত মজলিসও।
এদিকে জামায়াতসহ ইসলামী ঘরানার কয়েকটি দলের ঘোষিত আন্দোলনকে ভারত-সংশ্লিষ্ট নকশার অংশ বলছেন বিশ্লেষকদের বড় একটি অংশ। তাদের ভাষ্য, ‘ফ্যাসিস্ট’ হাসিনার পতন ভারত (India) কোনোভাবেই মেনে নিতে পারেনি; শেখ হাসিনা দেশ ছাড়ার পর থেকেই অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের বিরুদ্ধে নানামুখী কৌশল চালু করেছে তারা। প্রথমে সংখ্যালঘু নির্যাতনের অভিযোগ উসকে দেওয়া, আন্তর্জাতিক অঙ্গনে অপপ্রচার, পরবর্তীতে শ্রমিক আন্দোলনকে অস্থিরতায় ঠেলে দেওয়া—এসব দিয়ে লক্ষ্যভ্রষ্ট করার চেষ্টা হয়। আনসার বিদ্রোহ, সচিবালয়ে অশান্তি সৃষ্টির মতো ইস্যু উস্কে দিয়ে ড. ইউনূসের নেতৃত্বাধীন সরকারের পতনের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়েছে বলে তাদের দাবি। এখন, ফেব্রুয়ারির প্রথমার্ধে নির্বাচনের সময়সূচি ধরা হওয়ার পর ‘ইন্ডিয়া’ নির্বাচন বানচালের নতুন কৌশলে নেমেছে—ব্যাপক নাশকতার প্ররোচনা ও বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে কয়েকটি দলকে রাজপথে নামানো—এ দুই ট্র্যাকে। আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সতর্ক অবস্থান আর প্রধান দল বিএনপি’র নেতা-কর্মীদের তৎপতার কারণে ঝটিকা মিছিল ও হামলার ধারা থমকে গেলেও আসন্ন দুর্গাপূজাকে কেন্দ্র করে অস্থিতিশীলতার চেষ্টা থাকতে পারে—সরকারও সেক্ষেত্রে সতর্ক। বিশ্লেষকদের মতে, জামায়াতসহ ইসলামপন্থী দলের ঘোষিত কর্মসূচি এই দ্বিতীয় কৌশলের সঙ্গেই মিলে যায়।
এই প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক বিশ্লেষক ডা. জাহেদ উর রহমান বলেন, দেশে নির্বাচনের সুস্পষ্ট রোডম্যাপ ঘোষণার পর জাতীয় পার্টিকে নিষিদ্ধ করার তৎপরতা কোনো স্বাভাবিক রাজনৈতিক প্রক্রিয়া নয়; বরং পরিকল্পিতভাবে নির্বাচনী পরিবেশ জটিল করার অংশ। তার ভাষায়, পিআর ‘ভারতীয়’ একটি এজেন্ডা—এটি বাস্তবায়ন ও জাতীয় পার্টি নিষিদ্ধ করার দাবিসহ মিলিয়ে দেখলে নির্বাচন বানচালের বড় ষড়যন্ত্রই প্রতীয়মান হয়; ফ্যাসিবাদবিরোধী সকল শক্তির ঐক্য জরুরি, নইলে বড় দুর্যোগ নেমে আসতে পারে। একইসঙ্গে, জামায়াতসহ চার দলের কর্মসূচির দাবির তালিকায় জুলাই সনদ বাস্তবায়ন ও ফেব্রুয়ারিতে পিআরভিত্তিক নির্বাচন এবং জাতীয় পার্টি-সহ ১৪ দল নিষিদ্ধের বিষয়টি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।
অন্যদিকে, জুলাই সনদ বাস্তবায়ন নিয়ে দীর্ঘদিনের আলোচনায় সর্বশেষ ১৪ সেপ্টেম্বরের বৈঠকে মতবিরোধ অনেকটাই কমেছে বলে জানা যায়। বিএনপিও তাদের অনড় অবস্থান থেকে সরে এসে বাস্তবায়নের পদ্ধতি নির্ধারণের ভার সরকারকে দিয়েছে। সরকার চায় সব দলের সমঝোতা বা ঐকমত্য। ঐকমত্য কমিশনের সভাপতি ও প্রধান উপদেষ্টা ড. মুহাম্মদ ইউনূস (Dr. Muhammad Yunus) বলেন, জুলাই সনদের বিষয়ে সমঝোতায় আসতেই হবে—এ থেকে বেরোনোর উপায় নেই; সব দলের ঐকমত্য নিয়েই তিনি আশাবাদী। এই পরিস্থিতিতে রাজপথমুখী আন্দোলনের পেছনে অন্য কোনো সূক্ষ্ম উদ্দেশ্য কাজ করছে—এমন আশঙ্কাও উচ্চারিত হচ্ছে। তদুপরি পিআর প্রসঙ্গে জামায়াতের দাবি ঐকমত্য কমিশন ও নির্বাচন কমিশন আগেই বাতিল করেছে—এ নিয়ে আলোচনার সুযোগ নেই বলেই মত। বিশ্লেষক পিনাকী ভট্টাচার্য পিআরকে ‘সুস্পষ্ট ভারতীয় এজেন্ডা’ আখ্যা দিয়ে বলেন, ‘ফ্যাসিস্ট’ হাসিনাকে রাজনৈতিকভাবে টিকিয়ে রাখতে ভারত জামায়াতের মাধ্যমে পিআর-নির্বাচনের ইস্যু মাঠে এনেছে; এখন আরও কিছু দল তাতে সুর মিলিয়েছে। তার মতে, জামায়াত যদি সত্যি এ দাবিতে নামেই, সেটি তাদের জন্য ভয়ানক ক্ষতির কারণ হতে পারে; আর কেবল চাপ সৃষ্টি করে রাজনৈতিক ফায়দা তুলতে চাইলে কতদূর এগোবে—তাও ভাবার বিষয়। ‘সুযোগসন্ধানীরা’ অপেক্ষায় আছে বলে তার সতর্কবার্তা—সামান্য ভুল দেশের জন্য বড় ক্ষতি ডেকে আনতে পারে।
শুধু পিআর নয়, ‘জাতীয় পার্টি’ নিষিদ্ধ করার দাবিকেও অনেকে নতুন রাজনৈতিক চাল হিসেবে দেখছেন। ডাকসুর সাবেক ভিপি নুরুল হক নুরের দল গণঅধিকার পরিষদ ও এবি পার্টি এ দাবিতে সোচ্চার; সম্প্রতি জামায়াতও তাতে একাত্ম হয়েছে। এ দাবিতে আন্দোলনের মধ্যে নুরের ওপর হামলার ঘটনাকে তার দল ‘প্রাণনাশের চেষ্টা’ বলছে; আবার কেউ কেউ এর নেপথ্যে অন্য ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত দেখছেন—আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর বাইরে তৃতীয় পক্ষের সংশ্লিষ্টতার কথাও উচ্চারিত হচ্ছে। ফলে জামায়াতসহ দলগুলো মাঠে নামলে ‘তৃতীয় পক্ষ’ নাশকতার সুযোগ নেবে কি না—এ আশঙ্কা থেকেই যাচ্ছে; এতে আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটতে পারে।
দেশের চলমান প্রেক্ষাপটে জাতীয় স্বার্থে রাজনৈতিক ঐক্য জরুরি—এ কথা বলছেন নেতা ও বিশ্লেষকরা। তাদের মতে, ছাত্র–জনতার গণঅভ্যুত্থানকে নস্যাৎ করার চেষ্টা চলছে; দেশবিরোধী ষড়যন্ত্রও সক্রিয়। এসব রুখতে সব দলের ঐক্য ও ঘোষিত সময়ে সুষ্ঠু নির্বাচন অপরিহার্য; অন্যথায় ফ্যাসিবাদী শক্তিই লাভবান হবে। বিএনপির শীর্ষ নেতৃত্বের অভিমত—সংস্কারের দাবিগুলো বাহ্যিকভাবে যৌক্তিক শোনালেও অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য নির্বাচন বিলম্বিত করা; নীতিনির্ধারকরা এটিকে ‘ষড়যন্ত্র ও কৌশল’ হিসেবেই দেখছেন। বিএনপির স্থায়ী কমিটির সদস্য সালাহউদ্দিন আহমেদ বলেন, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের ঐক্যে ফাটল ধরানোর চেষ্টা হচ্ছে; সংস্কার নিয়ে আমরা আলোচনা করছি, কিন্তু নির্বাচনকে ঘিরে কেউ কেউ ধোঁয়াশা তৈরি করছে—এটা নির্বাচন বানচালের গভীর ষড়যন্ত্র; সবার সতর্ক থাকা প্রয়োজন।”
এদিকে পিআর দাবিকে ঘিরে বাড়ছে আরেক বিতর্ক—এটি কেবল নির্বাচনী সংস্কার নয়, বরং কৌশলগত রাজনৈতিক পরিকল্পনার অংশ। বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, এর লক্ষ্য দুর্বল, জোটনির্ভর ও সহজেই ভেঙে পড়া সরকার প্রতিষ্ঠা; তাতে অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ঝুঁকির মুখে পড়বে এবং প্রতিবেশী শক্তি India (ভারত) আরও প্রভাব বিস্তারের সুযোগ পাবে। উদাহরণ হিসেবে টানা ওঠে নেপালের সাম্প্রতিক অভিজ্ঞতা—সরাসরি ভোট (FPTP) ও পিআর মিলে ‘মিশ্র’ ব্যবস্থায় ছোট ছোট দলের প্রভাব বেড়েছে, বারবার জোট সরকার গড়লেও দ্রুত ভেঙেছে; কেবিনেট অদলবদল, নীতির অচলাবস্থা ও সামাজিক অস্থিরতা প্রায় নিয়মে পরিণত। বাংলাদেশের মতো বিভক্ত ভোটপ্যাটার্ন থাকলে পিআর চালু হলে বড় দলগুলোকে বাধ্যতামূলক জোটে টিকে থাকতে হবে—যার ভঙ্গুরতা দেশকে স্থিতিহীনতার দিকে ঠেলে দিতে পারে, বিদেশি প্রভাবের জানালাও বড় করে দিতে পারে।
পিআর দাবির স্থানীয় গতিপথ নিয়েও প্রশ্ন আছে। যে মহল দীর্ঘদিন আওয়ামী লীগ (Awami League)-এর পাশে ছিল—তারা খোলস বদলে গণআন্দোলনের স্লোগান তুলে পরে পিআর দাবিকে ত্বরান্বিত করে। ইসলামি দলগুলোর ঐক্যের ডাককে সামনে রেখে ধীরে ধীরে জামায়াতও এতে সম্পৃক্ত হয় এবং শেষ পর্যন্ত পিআর তাদেরও মুখ্য দাবিতে পরিণত হয়। সমালোচকদের মতে, এমন কৌশল প্রায়শই সংখ্যালঘু শক্তি ও কুচক্রী জোটনির্ভরতায় দেশকে জিম্মি করে। ইতিহাসের রেফারেন্স টেনে বলা হচ্ছে—উপমহাদেশে ‘নিজেদের পক্ষের’ সরকার ব্যর্থ হলে ভারত প্রপোরশনাল রিপ্রেজেন্টেশন তত্ত্বকে সামনে এনে স্থিতিশীল সরকারকে দুর্বল করার পথ খোঁজে; ঘনঘন সরকার পরিবর্তনে ‘ইনফ্লুয়েন্স ভ্যাকুয়াম’ তৈরি হয়, যেখানে প্রতিবেশীরা নিজেদের স্বার্থে প্রভাব খাটায়। হতাশ জনমত পরে পূর্বতন কর্তৃত্ববাদী কাঠামোকেই ‘স্বাভাবিক’ মনে করতে শুরু করে—এমন ঝুঁকির সতর্কতা দিচ্ছেন অনেকে।
সব মিলিয়ে, তাত্ত্বিকভাবে আকর্ষণীয় শুনালেও বাংলাদেশের বাস্তবতায় পিআর গুরুতর ঝুঁকি বয়ে আনতে পারে—নেপালের অভিজ্ঞতা অন্তত সেটিই বলে। প্রশ্নটা তাই ঘুরেফিরে একই জায়গায়—পিআরের মতো ইস্যু হঠাৎ কে সামনে আনল, কার ইন্ধনে? সংস্কার কমিশনের আলোচ্যসূচিতে না থাকা বিষয়টি কীভাবে মাঠ গরম করল? সমালোচকদের অভিযোগ, আওয়ামী লীগ ও ভারত (India)-এর প্ররোচনায় ড. ইউনূসের নেতৃত্বে নির্বাচনী প্রক্রিয়া বানচালের আঁচ মিলতেই জামায়াত এই ইস্যুকে নতুন আঙ্গিকে উসকে দিয়েছে—আগুনে ঘি ঢালার মতো। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি এখনো অনুত্তরিত—ইন্ধন যোগাচ্ছে আসলে কে?—এসব বিষয়ে স্বচ্ছ তদন্ত ও স্পষ্ট ব্যাখ্যাই সময়ের দাবি।