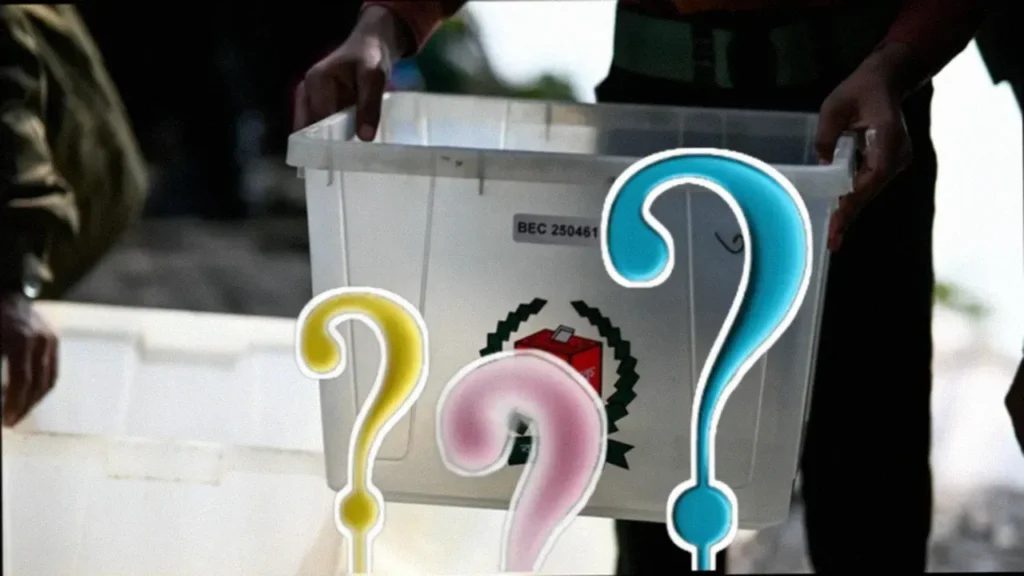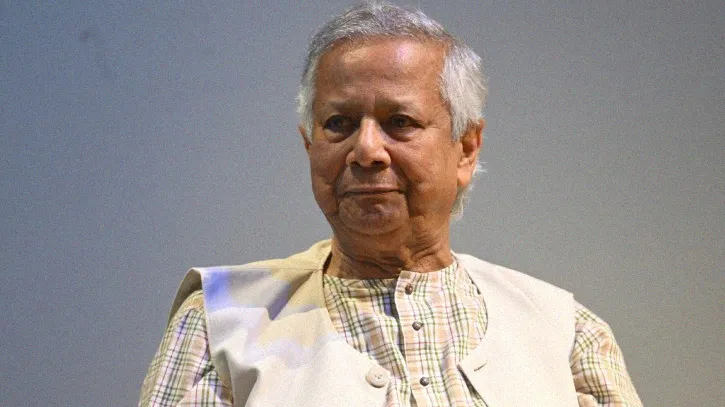জাতীয় সনদ নিয়ে যারা সরব, তাদের দাবি এখন নানা প্রশ্নে ঘেরা। তারা চান সনদের আইনি ভিত্তি, কিন্তু কিভাবে সেই ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করা যায়—তা কেউই মুখে আনতে পারছেন না। একইভাবে, সনদের বাস্তবায়ন চান বলেও সংসদ ছাড়া আইনের ভীতির ওপর দাঁড়িয়ে সেটি করা সম্ভব কিনা, সে বিষয়ে তাদের মধ্যে নেই কোনো স্পষ্ট ধারণা।
আরও জটিলতা দেখা যাচ্ছে নির্বাচনের প্রশ্নে। জাতীয় সনদের ভিত্তিতে নির্বাচন চাওয়া হলেও, সনদে এমন কী আছে যা নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য—এ বিষয়ে কোনো ব্যাখ্যা কেউ দিতে পারেননি। নভেম্বরে গণভোট আয়োজনের দাবিও তোলা হয়েছে, কিন্তু কেন নভেম্বরে তা জরুরি, সে ব্যাখ্যাও কারও কাছে নেই।
নির্বাচনে অংশগ্রহণের শর্ত হিসেবে পি.আর. (Proportional Representation) ব্যবস্থার কথা বলা হচ্ছে। যদিও উচ্চকক্ষে এ নিয়ে তেমন আপত্তি নেই, তবু বাংলাদেশের বাস্তবতায় নিম্নকক্ষে এই ব্যবস্থা কার্যকর নয়—তা সবাই জানলেও অনেকে না বোঝার ভান করছেন। আরও বিস্ময়কর হলো, সনদের অধ্যাদেশে প্রেসিডেন্টের বদলে প্রধান উপদেষ্টার সই লাগবে—এমন দাবিও এসেছে। অথচ বাংলাদেশের আইনে প্রধান উপদেষ্টার সইয়ের কোনো সাংবিধানিক মূল্য নেই, সেটি যেন কেউ বিবেচনায় নিচ্ছেন না।
এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নির্বাচনী প্রতীক ও কমিশনের ভূমিকা নিয়ে নতুন বিতর্ক। কেউ কেউ বলছেন, “শাপলা ছাড়া নির্বাচনে যাব না।” কিন্তু বর্তমান নির্বাচন আইনে কোনো রাজনৈতিক দলই নির্দিষ্ট কোনো প্রতীক একচেটিয়াভাবে দাবি করতে পারে না—এই বাস্তবতাও তাদের আলোচনায় অনুপস্থিত। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের নিরপেক্ষতা নিয়েও প্রশ্ন তোলা হচ্ছে, যেন যা তারা চায় তা না পেলে নিরপেক্ষতা হারায়—এই ভুল ধারণাই যেন ক্রমে গেঁথে যাচ্ছে তাদের অবস্থানে।
সব মিলিয়ে, জাতীয় সনদ ও গণভোট নিয়ে যতটা দাবি শোনা যাচ্ছে, তার তুলনায় উত্তর আসছে অনেক কম। যুক্তির জায়গা যেন ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে আবেগ ও রাজনৈতিক সুবিধার ভেতর।