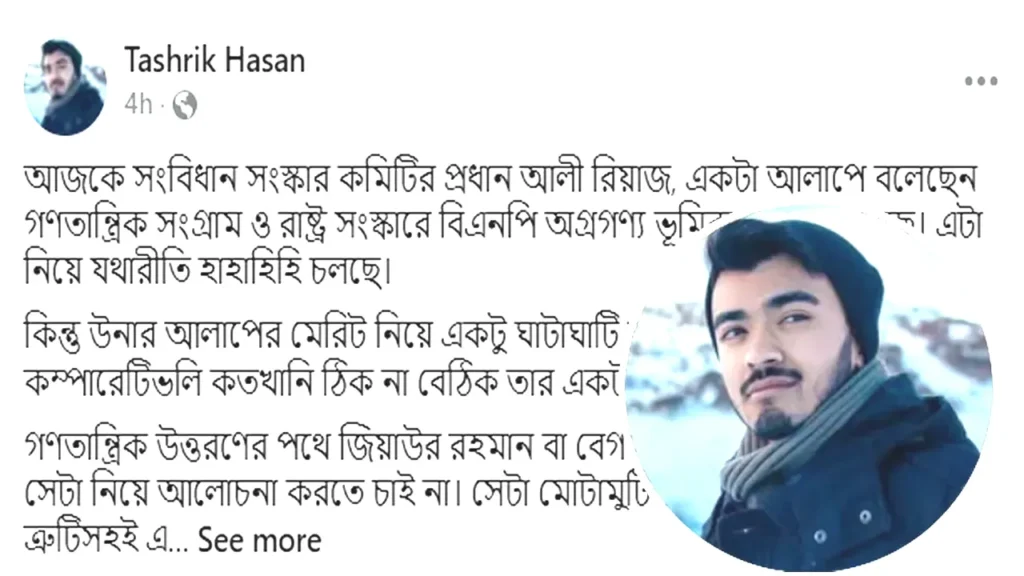সংবিধান সংস্কার ও রাষ্ট্রীয় পুনর্গঠনের প্রসঙ্গে আলী রিয়াজ (Ali Riaz) সম্প্রতি এক আলোচনায় বলেছিলেন, গণতান্ত্রিক সংগ্রামে ও রাষ্ট্র সংস্কারে বিএনপি (BNP) গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। তাঁর এই বক্তব্যকে ঘিরে সোশ্যাল মিডিয়ায় যেমন মজা-মশকরা হচ্ছে, তেমনি উঠছে গুরুতর প্রশ্নও—এই বক্তব্যের পেছনে বাস্তবতার ভিত্তি কতখানি?
রাজনৈতিক ইতিহাসের আলোকে চিন্তা করলে দেখা যায়, যেসব সিদ্ধান্ত একসময় বিরোধিতা বা বিতর্কের জন্ম দিয়েছিল, সেগুলোর কিছুই আজ রাষ্ট্রব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অংশ। যেমন, জিয়াউর রহমানের সময়কালের কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ, যেগুলোকে অনেকেই রাষ্ট্রীয় কাঠামো সংস্কারের মাইলফলক হিসেবে চিহ্নিত করেন।
সাম্প্রতিক বিতর্কের প্রেক্ষাপটে একদল বলছে, বিএনপিকে “রাষ্ট্র সংস্কারের কান্ডারী” হিসেবে চিহ্নিত করাটা অতিরঞ্জিত। কিন্তু যাঁরা ইতিহাস ঘাটেন, তাঁরা জানেন—জিয়াউর রহমান বিচার বিভাগকে সংসদের প্রভাব থেকে বের করে এনে সুপ্রিম জুডিশিয়াল কাউন্সিল (Supreme Judicial Council)-এর হাতে বিচারপতি অপসারণের ক্ষমতা দেন। এটি ছিল বিচার বিভাগের স্বাধীনতার পথে একটি মৌলিক পরিবর্তন। পরবর্তীতে এই ক্ষমতা আবার সংসদের হাতে ফিরিয়ে নিয়ে আসে আওয়ামী লীগ (Awami League) সরকারের সময়, যার পরিণতিতে প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহার দেশত্যাগের ঘটনা ঘটে—একটা বড় বিতর্কের জন্ম দিয়ে।
আরেকটি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ ছিল সংবিধানে গণভোটের বিধান সংযোজন, যা জনগণের সরাসরি মতামতের ভিত্তিতে আইন প্রণয়নের পথ খুলে দেয়। যদিও সাম্প্রতিক সময়ে বিএনপি এই গণভোট ব্যবস্থার বিপক্ষে অবস্থান নিয়েছে, যা কিছুটা বেমানান বলে মনে করছেন অনেকেই। প্রশ্ন থেকে যায়—জিয়াউর রহমান যেটাকে রাষ্ট্রকে গণমুখী করার প্রয়াস হিসেবে দেখেছিলেন, আজ তার উত্তরসূরিরা কেন সেই নীতির বিরোধিতা করছেন?
এদিকে খালেদা জিয়া (Khaleda Zia) তাঁর শাসনামলে সংসদীয় পদ্ধতির দিকে ফিরে যাওয়ার মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি শাসিত পদ্ধতি থেকে সরে আসেন, এবং রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার লক্ষ্যে কেয়ারটেকার সরকার ব্যবস্থাকেও স্বীকৃতি দেন। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ আইনসংশোধন ছিল, যেটি কিছুদিনের জন্য হলেও রাজনৈতিক আস্থার সংকট প্রশমনে সাহায্য করেছিল।
তবে এই তুলনামূলক আলোচনায় ‘মুজিব বংশ’ বা ‘আওয়ামী লীগের সংশোধনীগুলো’ কতটা জনমুখী ছিল—সে প্রশ্নও উত্থাপিত হচ্ছে। সমালোচকরা মনে করেন, একদলীয় শাসনব্যবস্থার পথ উন্মুক্ত করেছিল বাকশালের মত গঠন, যেখানে মত প্রকাশের স্বাধীনতা বা প্রতিষ্ঠানিক জবাবদিহিতা প্রায় অনুপস্থিত ছিল। যদিও আওয়ামী লীগের অনেক নেতা আজও এটাকে প্রয়োজনীয় ঐতিহাসিক বাস্তবতা হিসেবে তুলে ধরেন।
আলী রিয়াজের বক্তব্য যে বিতর্ক তৈরি করবে তা অনুমেয়ই ছিল, তবে সেটাকে পুরোপুরি ‘হাহাহিহি’ দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া হয়তো রাজনৈতিক ইতিহাসকে সরলীকরণ করা হয়ে যাবে। রাষ্ট্র সংস্কার তো নিছক কাগুজে নথির ব্যাপার নয়—এটা সময়োপযোগী রাজনৈতিক দূরদর্শিতার প্রকাশ। আর সে বিবেচনায় বিএনপির ভূমিকাকে একেবারে অস্বীকার করাও বাস্তবতাবিচ্যুতি হতে পারে।
ভাববার বিষয় হলো, কে কতটা পরিবর্তন এনেছে, আর সেই পরিবর্তন আদতে জনস্বার্থে ছিল কি না—এই বিশ্লেষণ করাটাই জরুরি, হাসিঠাট্টার বদলে।