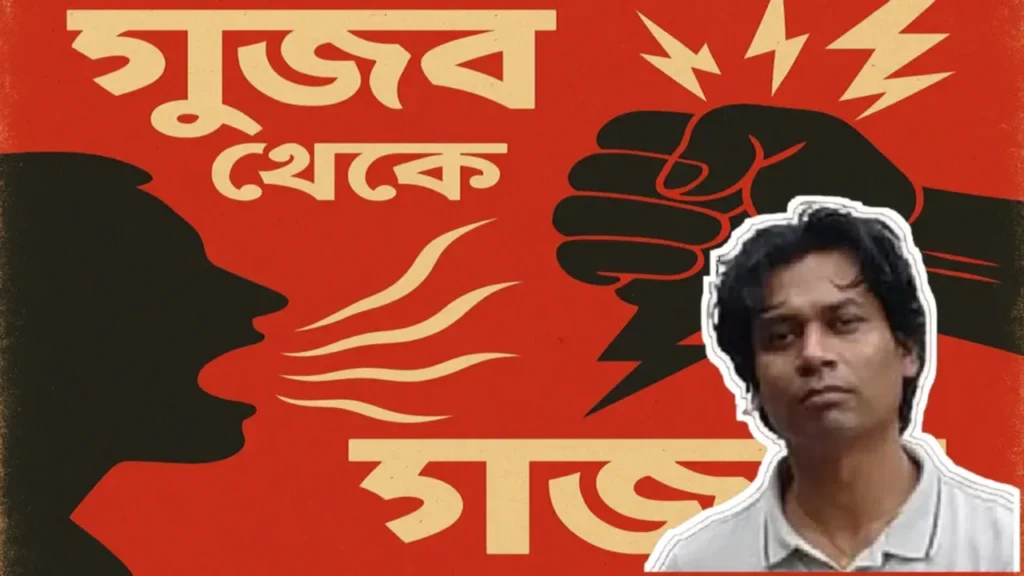বাংলাদেশসহ গোটা বিশ্বজুড়েই রাজনীতিতে এখন এক অদ্ভুত বাস্তবতা বিরাজ করছে—যেখানে সত্যের চেয়ে ‘দেখতে যেমন লাগে’ সেটাই বেশি গুরুত্বপূর্ণ। নির্বাচনপূর্ব বা পরবর্তী সময়ে হঠাৎ কোনো ইস্যুকে অতিরঞ্জিত করে তুলে ধরা, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে গুজব ছড়ানো কিংবা আবেগনির্ভর বক্তব্যে মানুষকে মোহিত করে ফেলা—এসব কৌশলেই গড়ে উঠছে এক ধরনের ‘হাইপার রিয়ালিটি’। এই বাস্তবতায় মানুষ সহজেই বিভ্রান্ত হয় এবং সত্য-মিথ্যার পার্থক্য নির্ণয়ের আগেই আবেগের বশে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।
এই রাজনৈতিক আবহে জনতুষ্টির রাজনীতির (Populism) জোয়ার আরও বেশি দানা বেঁধেছে। “সব সমস্যার সমাধান আমরা” টাইপের আবেগঘন প্রতিশ্রুতি, নীতিনির্ভর পরিকল্পনার অভাব, আর “তোমরা যা শুনতে চাও” সেটাই শোনানো—এসব মিলিয়ে এক ধরনের অবাস্তব রাজনীতি তৈরি হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, কারও বক্তব্য কাটছাঁট করে প্রচার করা হয় যাতে মনে হয় তিনি “দেশ বিক্রি করে দিয়েছেন” বা তিনি “নাস্তিক”; আবার অপরপক্ষে কোনো দলকে “শুধুই মুক্তির একমাত্র উপায়” হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা হয়, বাস্তব নীতিমালার প্রমাণ ছাড়াই।
রাজনৈতিক উত্তালতা বা বড় ধরনের টার্নিং পয়েন্টের সময় গুজবের মাত্রা আরও বেড়ে যায়। “অমুক দেশ সেনা পাঠাচ্ছে”, “তামুক নেতা পালিয়ে গেছেন”, “ভোটের ফলাফল আগে থেকেই নির্ধারিত”—এইসব বানোয়াট খবর মানুষের মনে ভীতির সঞ্চার ঘটায়। এবং উদ্বেগজনক ব্যাপার হলো, মানুষ সত্য-মিথ্যার যাচাই না করেই এসব গুজবে বিশ্বাস করে ফেলে এবং সেই আবেগ থেকেই ভোটের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়।
জনতুষ্টির রাজনীতির আরেক বৈশিষ্ট্য হলো—অবাস্তব, তাৎক্ষণিক লাভের প্রতিশ্রুতি। যেমন, “১০ টাকায় চাল”, “কাজ কম, বেতন সমান”, “আমাদের ভোট দিলে বেহেশত”—এসব স্লোগান বাস্তবতা বিবর্জিত হলেও আবেগে ভর করে জনগণের সমর্থন আদায় করে নেয়। এতে ভোটার দীর্ঘমেয়াদি নীতির চিন্তা না করে তাৎক্ষণিক লাভের মোহে পড়ে যায়।
গুজব, হাইপ ও আবেগনির্ভর কনটেন্ট খুব সহজেই ভাইরাল হয়। এগুলোর সেনসেশনালিজমের কারণে মানুষ দ্রুত শেয়ার করে এবং পরিবার-পরিজনের মধ্যেই বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে নেয়। অথচ এসব কনটেন্টের সত্যতা যাচাই করা হয় না। প্রান্তিক জনগোষ্ঠী যেমন তথ্য ও শিক্ষার অভাবে এসব ফাঁদে পড়ে, তেমনি শহরের শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণিও অনেক সময় উৎস যাচাই না করেই বিশ্বাস করে ফেলে।
এই প্রক্রিয়ায় ভোটারদের মনে গঠিত হয় আগাম সিদ্ধান্ত, যেটা গণতন্ত্রকে বিকৃত করে দেয়। যখন কোনো আংশিক বা সম্পূর্ণ মিথ্যা বয়ানকে দলীয় প্রচার, মিডিয়া কাঠামো ও সোশ্যাল মিডিয়ার বট বাহিনীর মাধ্যমে একমাত্র ‘সত্য’ হিসেবে দাঁড় করানো হয়, তখন তা সরাসরি গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়ায়। মানুষ নীতির ভিত্তিতে নয়, বরং একজন হাইপ-তোলা ‘নায়ক’ অথবা ‘শত্রুবিরোধী যোদ্ধা’কে ভোট দিতে শুরু করে।
এর সঙ্গে ধর্মীয় আবেগের রাজনীতিও যুক্ত হয়ে যায়। “আমাদের ভোট দিলে শরিয়াহ কায়েম হবে”, “বেহেশতে যাওয়ার রাস্তা খুলে যাবে”, “অন্যকে ভোট দিলে ইসলাম বিপন্ন”—এইসব বক্তব্য ধর্মকে রাজনৈতিক অস্ত্রে পরিণত করে। এর ফলে তিন ধরনের বিকৃতি ঘটে:
১) নীতিনির্ভর ভোটের জায়গায় আসমানি পুরস্কারের আশ্বাস উঠে আসে;
২) সমাজ ধর্মীয় বিভাজনে পড়ে—‘ভালো মুসলিম’ বনাম ‘সন্দেহজনক মুসলিম’;
৩) মতপ্রকাশ, সংখ্যালঘু অধিকার কিংবা নারীর অধিকারের কথা বললেই তাকে “নাস্তিক”, “বেহায়া” বা “বদ্মাশ” হিসেবে ট্যাগ দেওয়া হয়।
এটা গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি ও অন্তর্ভুক্তিমূলক রাজনীতির সম্পূর্ণ পরিপন্থী। এর সঙ্গে যুক্ত হয় বট বাহিনী, সাইবার বুলিং ও ভয়-ভীতির পরিবেশ। সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে সংগঠিত হুমকি, গালিগালাজ, অটো কমেন্ট—সব মিলিয়ে প্রশ্ন করলেই ব্যক্তিকে ‘রাষ্ট্রবিরোধী’, ‘ধর্মবিরোধী’ বা ‘দলদ্রোহী’ হিসেবে ঘোষণা দেওয়া হয়। এর ফলে একটি ‘সাইলেন্সড স্পেস’ তৈরি হয় যেখানে সাধারণ মানুষ ভয় পেয়ে মুখ বন্ধ করে ফেলে এবং হাইপনির্ভর বয়ানই একমাত্র সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠা পায়।
এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য প্রয়োজন তথ্য যাচাই, ডিজিটাল লিটারেসি এবং শক্তিশালী ফ্যাক্ট-চেকিং ব্যবস্থা। প্রযুক্তি সক্ষম, স্বচ্ছ এবং দ্রুতগতির ফ্যাক্ট-চেকিং প্ল্যাটফর্ম গড়ে তুলতে হবে—যারা ভাইরাল কনটেন্ট যাচাই করে সাধারণ ভাষায় মানুষের সামনে উপস্থাপন করবে এবং সহজে শেয়ারযোগ্য ফর্ম্যাটে তা সোশ্যাল ও মেইনস্ট্রিম মিডিয়ায় ছড়াবে।
স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও কমিউনিটি সেন্টারে শিক্ষার্থীদের শিখাতে হবে:
১) কে বলছে?
২) কোথা থেকে বলছে?
৩) কেন এখন বলছে?—এই প্রশ্নগুলো যেন তারা অভ্যাসগতভাবে করে।
আবার সেই সাথে ফেক পেজ, মিথ্যা স্ক্রিনশট, AI-জেনারেটেড ছবি-ভিডিও শনাক্ত করার বেসিক ধারণাও থাকা জরুরি।
রাজনৈতিক দল যদি সত্যিই গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে, তাহলে তাদের তিনটি অঙ্গীকার এখনই করতে হবে:
১) ধর্মকে ভোটের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার না করা,
২) অবাস্তব প্রতিশ্রুতি না দেওয়া,
৩) বট বাহিনী ও ট্রোলিং বন্ধে নিজস্ব অবস্থান পরিষ্কার করা।
এছাড়া মিডিয়া ও টকশোগুলোর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তোলা জরুরি। TRP নির্ভর হাইপ তৈরির শিরোনামের পরিবর্তে প্রেক্ষাপট-ভিত্তিক বিশ্লেষণ এবং গুজব ছড়ানো নেতাদের অযথা প্ল্যাটফর্ম না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে। নির্বাচনের সময়ে ফ্যাক্ট-চেকিং সেগমেন্ট বাধ্যতামূলক করা উচিত।
হাইপ, গুজব ও জনতুষ্টির রাজনীতি শুধু কিছু কৌশলগত সমস্যা নয়—এগুলোই আসলে গণতন্ত্রের ভিত ধ্বংস করে দেয়। এতে মানুষ ভোট দেয় না আইন, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, মানবাধিকার কিংবা অর্থনীতির ভিত্তিতে; বরং আবেগ, ভয় ও গুজবের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নেয়।
দীর্ঘমেয়াদে এই রাজনৈতিক সংস্কৃতির ফল ভয়াবহ: প্রশ্নহীন নেতৃত্ব, দুর্বল প্রতিষ্ঠান, বিভক্ত সমাজ এবং নিরাপত্তাহীন সংখ্যালঘু ও দুর্বল ভোটারগোষ্ঠী।
গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখতে হলে আজই প্রয়োজন— তথ্য যাচাইয়ের অভ্যাস, ডিজিটাল শিক্ষার বিস্তার, নীতিনির্ভর রাজনীতির চর্চা, এবং ধর্ম, জাতি, লিঙ্গ ও আবেগকে রাজনৈতিক অস্ত্র বানানোর প্রবণতা থেকে সরে আসা।
নইলে হাইপনির্ভর হিরোরা আসবে-যাবে, কিন্তু গণতন্ত্র শুধু কাগজে থাকবে—বাস্তবে নয়।