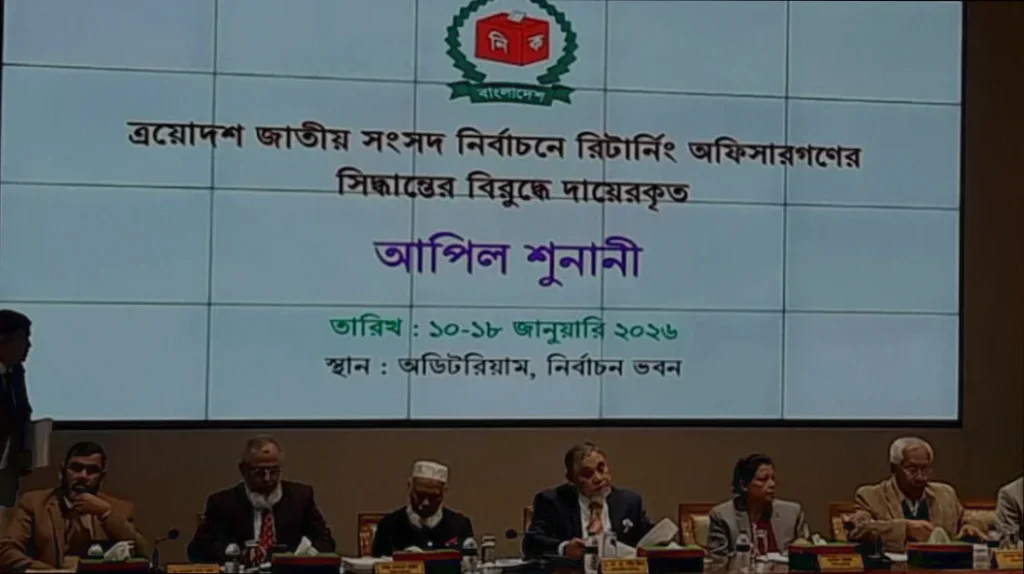সংসদের উচ্চকক্ষ গঠন নিয়ে চলমান বিতর্কে বিএনপি (BNP) অন্তর্বর্তী সরকারের আহ্বান প্রত্যাখ্যান করেছে—এমন সিদ্ধান্ত অনেকের চোখে বিতর্কিত মনে হলেও, বাস্তবতা বলছে এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক ও সাংবিধানিক প্রেক্ষাপটে যথার্থ এবং সময়োপযোগী। সরকারের প্রস্তাব ছিল, সংসদের উচ্চকক্ষ গঠনের ক্ষেত্রে সংখ্যানুপাতিক প্রতিনিধিত্ব বা PR (Proportional Representation) পদ্ধতি গ্রহণ করা হোক, যেখানে দলগুলোর প্রাপ্ত ভোটের অনুপাতে আসন বণ্টন হবে। তবে বিএনপি সুস্পষ্ট ভিন্নমত জানিয়ে এই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছে।
৩১ আগস্ট রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবন যমুনায় অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা ও উপদেষ্টামণ্ডলীর সঙ্গে বৈঠকে বিএনপির প্রতিনিধিরা স্পষ্ট করে বলেন, পিআর পদ্ধতিতে উচ্চকক্ষ গঠনের কোনো সাংবিধানিক বা রাজনৈতিক বৈধতা নেই। তাদের যুক্তি, এটি বাস্তবায়নযোগ্য নয় এবং বাংলাদেশ এখনো সেই পর্যায়ে পৌঁছেনি যেখানে পিআর ভিত্তিক রাজনৈতিক কাঠামো কার্যকর হতে পারে।
বিএনপির অবস্থান: রাজনৈতিক ভারসাম্য না নকল প্রতিচ্ছবি?
বিএনপি (BNP)-র মতে, পিআর পদ্ধতির মাধ্যমে উচ্চকক্ষ গঠিত হলে তা নিম্নকক্ষের একটি প্রতিচ্ছবিতে পরিণত হবে, অর্থাৎ দুই কক্ষেই একই দল বা জোটের আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পাবে। এতে উচ্চকক্ষ গঠনের মূল উদ্দেশ্য—সাংবিধানিক ভারসাম্য ও ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ—নষ্ট হবে। তারা চাইছে, একটি দল নিম্নকক্ষে যেভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তার ভিত্তিতেই উচ্চকক্ষে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারিত হোক। এর মাধ্যমে সরকার গঠনের মত নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা না থাকলেও বিরোধী মত ও বিকল্প কণ্ঠের অবস্থান উচ্চকক্ষে স্পষ্ট হবে।
তাদের আরও যুক্তি, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রথিতযশা ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিদের উচ্চকক্ষে অন্তর্ভুক্ত করার সুযোগ থাকা উচিত—যা পিআর পদ্ধতির যান্ত্রিক কাঠামোতে কার্যত সম্ভব নয়।
সংবিধানিক ও রাজনৈতিক বাস্তবতা: পিআর কি বাংলাদেশের জন্য প্রস্তুত?
অনেকেই বলছেন, বাংলাদেশের বর্তমান রাজনৈতিক সংস্কৃতি এখনো ততটাই পরিপক্ব নয় যেখানে নিখুঁত পিআর ভিত্তিক একটি সংসদ কাজ করতে পারবে। ইতিহাস বলছে, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে পারস্পরিক আস্থার ঘাটতি, প্রাতিষ্ঠানিক শক্তির দুর্বলতা এবং প্রভাবশালী দলগুলোর ক্ষমতা কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি এমন একটি ব্যবস্থা কার্যকর হওয়ার পথে বড় বাধা। একটি যুক্তি হলো—যেখানে গ্রহণযোগ্য নির্বাচনে কোনো দলই ৫০ শতাংশ ভোট পায় না, সেখানে PR ব্যবস্থা কার্যকর হলে উচ্চকক্ষে একগুচ্ছ ছায়া-দলীয় প্রতিনিধিত্ব তৈরি হবে, যারা মাঠ পর্যায়ে কোনো জনসম্পৃক্ততা ছাড়াই সিদ্ধান্ত গ্রহণে যুক্ত থাকবে।
এছাড়া, উচ্চকক্ষ গঠনের প্রস্তাব যদি ব্যয়বহুল এবং অকার্যকর হয়, তা দেশের সামষ্টিক অর্থনীতির ওপরও চাপ ফেলতে পারে। এসব দিক বিবেচনায় বিএনপির বাস্তববাদী অবস্থান অনেক বেশি সময়োপযোগী ও দায়িত্বশীল।
বিভক্ত রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি
জামায়াতে ইসলামি ও জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি) বিএনপির ভিন্নমতের বিরোধিতা করেছে। তারা মনে করছে, বিএনপির চাওয়া অনুযায়ী না হলে তারা জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের বিষয়েও আপত্তি জানাবে। তবে এখানেও প্রশ্ন উঠছে—একটি সনদ বাস্তবায়নে জোর করে সংখ্যা দিয়ে মত চাপিয়ে দেওয়া কি গণতান্ত্রিক?
জাতীয় ঐকমত্য কমিশন (National Consensus Commission)-এর সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, উচ্চকক্ষে পিআর পদ্ধতি প্রয়োগে কোনো দল একক সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না, এটাই প্রস্তাবের মূল প্রেরণা। কিন্তু বাস্তবতা হলো—প্রস্তাবিত কাঠামোতে যে দলের ভোট বেশি, তাদেরই প্রক্সি নিয়ন্ত্রণ থাকবে। এটা ভারসাম্য নয়, বরং দুর্বল অনুকরণ।
সংসদ গবেষক অধ্যাপক নিজাম উদ্দিন আহমদ উচ্চকক্ষ নিয়ে ঐকমত্য কমিশনের সিদ্ধান্তকে প্রশংসনীয় বলে মত দিলেও, বিএনপির প্রস্তাবকে অযৌক্তিক বলে উড়িয়ে দিয়েছেন। কিন্তু তিনি যা উপেক্ষা করেছেন তা হলো—ভবিষ্যৎ সংসদ যেন শুধু সংখ্যার খেলা না হয়ে যায়, সেটাই বিএনপির মূল লক্ষ্য।
বিএনপির অবস্থান শুধু দলীয় স্বার্থরক্ষার জন্য নয়, বরং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক, যুক্তিনির্ভর এবং সংবিধানসম্মত কাঠামো নিশ্চিত করার প্রয়াস। যে দেশে একদলীয় রাজনীতির ইতিহাস এখনো তাজা, যেখানে তত্ত্বাবধায়ক সরকার বাতিলের মতো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এককভাবে গ্রহণ করা হয়—সেখানে উচ্চকক্ষে ভারসাম্যহীনতা আরেকটি রাজনৈতিক বিপর্যয়ের দ্বার উন্মুক্ত করতে পারে।
ভবিষ্যৎ সংসদের মাধ্যমেই হতে হবে সাংবিধানিক সংস্কার
বিএনপি স্পষ্ট বলেছে—সংবিধান সংশোধন ও উচ্চকক্ষ গঠনের মতো বড় সিদ্ধান্ত আগামী সংসদের মাধ্যমেই হওয়া উচিত। কেননা, গণভোট বা রাষ্ট্রপতির ঘোষণায় এমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বাস্তবায়ন করা সাংবিধানিক শুদ্ধতার পরিপন্থী হতে পারে। এটাই সুস্থ গণতন্ত্রের পথ।
সবদিক বিবেচনায়, পিআর পদ্ধতির প্রতি বিএনপির আপত্তি হঠাৎ আবেগপ্রসূত কোনো সিদ্ধান্ত নয়—বরং এটি বাংলাদেশের রাজনৈতিক বাস্তবতা, সাংবিধানিক সুস্থিতি এবং ভবিষ্যৎ দায়বদ্ধতাকে মাথায় রেখেই নেওয়া একটি সুপরিকল্পিত অবস্থান।